শ্রীহট্ট শহরে দুর্গাপূজার ইতিবৃত্ত

সুদীর্ঘকালের বর্ণিত ইতিহাসে জানা যায়, শ্রীহট্টে রাজা গৌর গোবিন্দের শাসনকাল এবং তার আগেই শক্তি পূজার প্রচলন ছিল। ভৌগোলিকভাবে বিবেচনা করলে দেবীর ৫১ সতীপীঠের মধ্যে গ্রীবাপীঠ ও জয়ন্তীপীঠ এই শহরের কাছেই অবস্থিত। রাজা গৌর গোবিন্দ নিজেও শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি শৈশবে কামাক্ষ্যা মন্দিরে অবস্থান করেন এবং টোল শিক্ষালাভ শেষে শ্রীহট্টে ফিরে আসেন। যুদ্ধপরাজিত হলে তার সঙ্গেই অনেক স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন জায়গায় নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হন। ফলে সমাজে আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপে স্থবিরতা দেখা দেয়।
১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ইংরেজ শাসনকালে পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞাসমূহ শিথিল হলে হিন্দুরা আবারও একত্রিত হয়ে দুর্গাপূজা উদযাপন শুরু করেন। তারই ধারাবাহিকতায় মহারাজা নবকৃষ্ণ রায়ের উদ্যোগে শোভাবাজার রাজবাড়িতে জাঁকজমকভাবে সার্বজনীন দুর্গাপূজার সূচনা হয়, যা আজও চলমান।
সেই ধারায় বাণিজ্য, ব্যবসা ও সামাজিকতার প্রসার ঘটে। অর্থনীতির নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। বাণিজ্যের খোঁজে উদ্যোক্তারা কেউ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আবার কেউ শ্রীহট্টে আগমন করেন। তাদেরই একজন উদ্যোক্তা বলরাম বাবু প্রথমে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে চুনাপাথরের ব্যবসার খোঁজে ছাতকে আসেন।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, সেখানে তার ছেলে বাঞ্চারাম বাবুর মাধ্যমে পারিবারিকভাবে দুর্গাপূজার সূচনা হয়। পরবর্তীতে তার ছেলে ব্রজগোবিন্দ বাবু জমিদারি ক্রয় করে ব্যবসার সূত্রে সিলেটে আসেন ১৮০৯ সালের দিকে এবং ১৮১০ সালে শহরে জাঁকজমকভাবে পূজার আয়োজন শুরু করেন শেখঘাটের লাল ব্রাদার্সের বাড়িতে। সেখানে মাসব্যাপী আনন্দযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।
তার পুত্র বঙ্কবাবু, যিনি সত্যিকার অর্থেই দানবীর হিসেবে খ্যাত এবং আধুনিক সিলেট নগরীর রূপকার হিসেবে পরিচিত, তার সময় পূজার ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রজাদের উপহার দেওয়া হতো, ওড়িষ্যা থেকে পুরোহিত, কাশী ও লক্ষ্ণৌ থেকে বিখ্যাত বাইজিরা আরতি করতে আসতেন এবং প্রতিদিন শতাধিক পদ রান্না হত সবার জন্য।
১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজকুমার সেন সিলেটের নয়াসড়কে নিজ পৈতৃক ভিটেবাড়িতে প্রথমবার দুর্গাপূজার প্রচলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে জাস্টিস রনধীর সেন ও আইনজীবী দেবাশীষ সেনের সুযোগ্য উত্তরসূরিরা সেই ঐতিহ্য আজও বজায় রাখছেন। দীগেশ ঘোষের পিতা গিরিশ ঘোষ এবং তার দাদা ১৮৪০-এর দিকে দুর্গাপূজা শুরু করেন। ১৯৩৫ সালের দিকে এই বাড়িতেই সর্বপ্রথম জোড়-কাঠামোর প্রতিমা গড়ে পূজা শুরু হয়। পরে তা হাওয়াপাড়ায় নিজ বাসভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং আজও সেখানে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নয়াসড়কের চৌধুরী পরিবার, যা খাজাঞ্চী বাড়ী নামে পরিচিত, তাদের পারিবারিক দুর্গাপূজা ব্রিটিশ আমল থেকেই সুপরিচিত। নগেন্দ্র চৌধুরীর সময় থেকে এই পূজা শহরজুড়ে আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। সুবিদবাজারের দস্তিদার বাড়িতেও একসময় বিশাল আয়োজনে পূজা হতো।
পরবর্তীকালে বিভিন্ন ছোট-বড় জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ এস্টেটে পূজা শুরু করেন সার্বজনীন রূপে। ৪০-এর দশক পর্যন্ত এটি ছিল জমিদার ও প্রজাদের এক আত্মিক বন্ধনের উৎসব। তৎকালীন হিন্দু জমিদারদের আতিথেয়তা ও দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় শারদীয় উৎসবের মাঝে। সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পূজার সূচনা হয় দাড়িয়াপাড়ায় প্রয়াত শশাঙ্ক দাশ পুরকায়স্থের (মোক্তার) বাড়িতে, কালীঘাটে গণেশ মহাজনের বাড়িতে, চৌহাট্টায় সেন্ট্রাল ফার্মেসির বাসায়, জামতলার দেবেন্দ্র মহাজনের বাড়ি এবং শিবগঞ্জে প্রয়াত সুধীর দে’র বাড়িতে। এভাবেই মহল্লায় মহল্লায় বারোয়ারি পূজার সূচনা হয় এবং তা আজও চলমান।
১৯৪৭ ও ১৯৭১-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীরা দেশত্যাগ করেন, ফলে দস্তিদার ও খাজাঞ্চী বাড়ী মতো অনেক পূজা বন্ধ হয়ে যায়। তবুও শ্রীহট্টের আদি লাল ব্রাদার্স, নয়াসড়কের সেনবাড়ি ও ঘোষবাড়ির পূজা শত বছরের ঐতিহ্য মেনে আজও সকল বাধা অতিক্রম করে মাতৃআরাধনা করে যাচ্ছে।
লেখক :
সুবিন সৌর
অনলাইন এক্টিভিস্ট
তাহির আহমদ
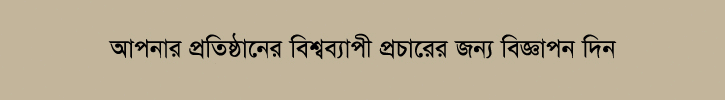
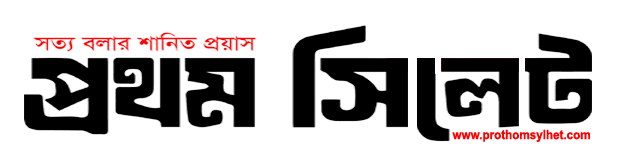
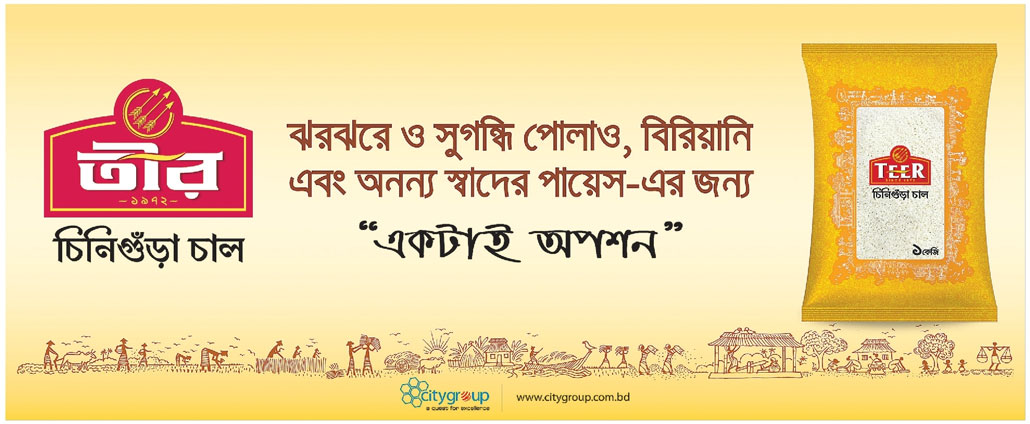
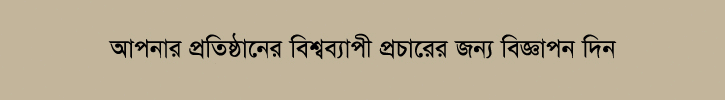

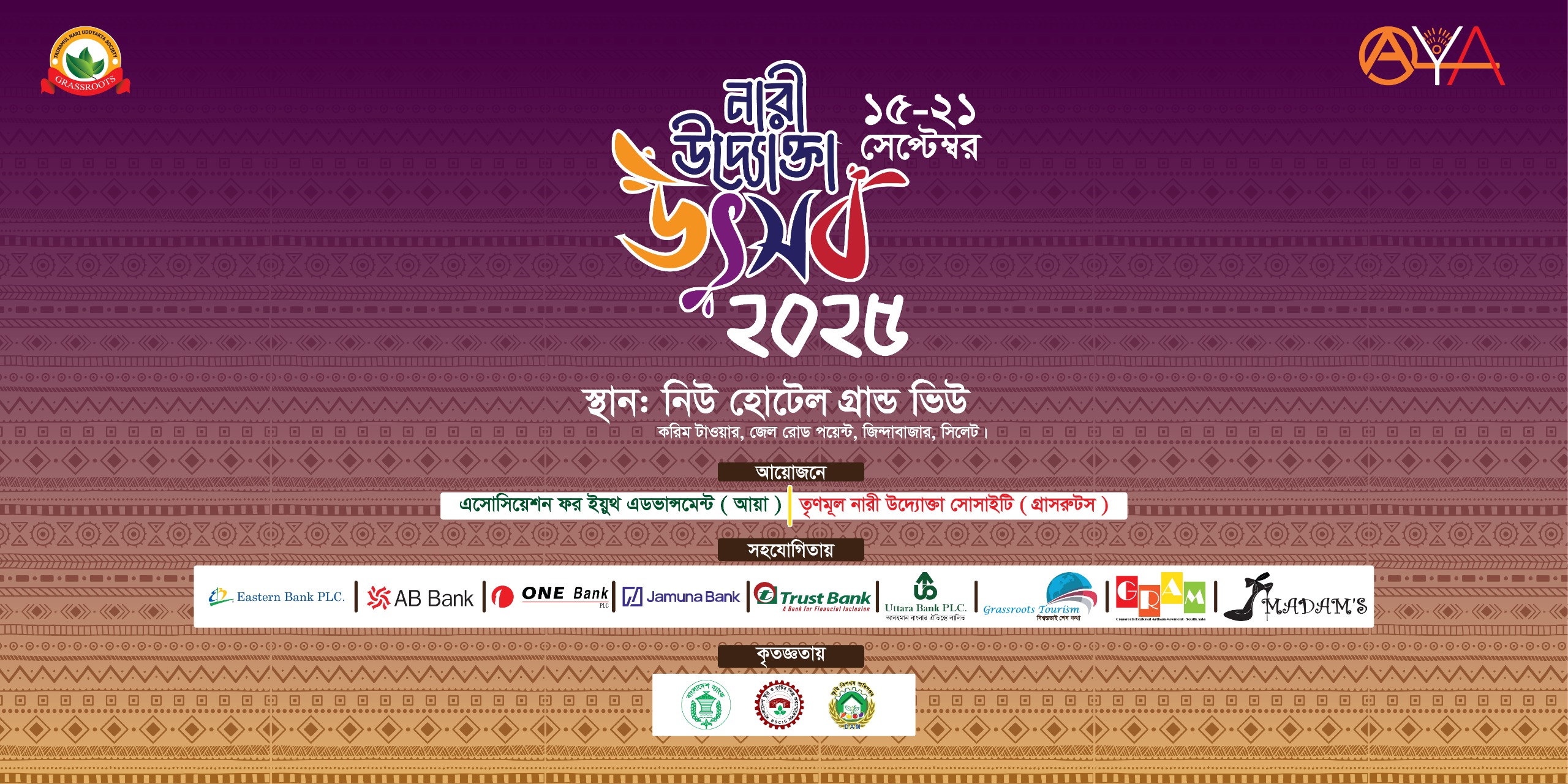




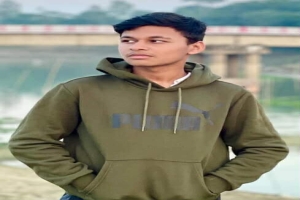
মন্তব্য করুন: