নোয়াখালি’ থেকে ‘মৌলভীবাজার’ নামকরণের ইতিহাস
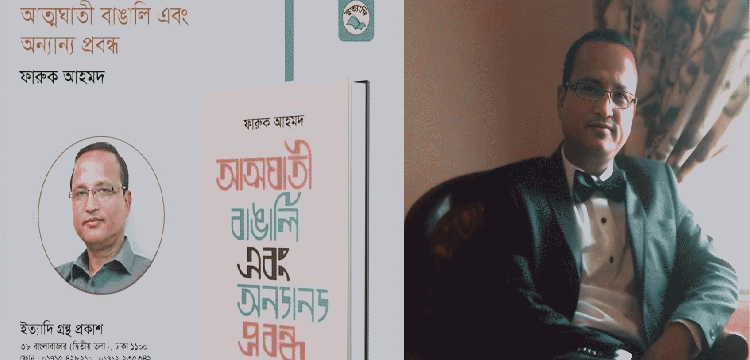
মৌলভীবাজার এ নামটি খুব প্রাচীন নয়। ‘মৌলভী’ শব্দটি অনেক অর্থ বহন করে। আগেকার দিনে বঙ্গদেশে শিক্ষিত, এমনকি সম্ভান্ত মুসলমানদের নামের আগে সম্মানার্থে ‘মৌলভী’ উপাধিটি ব্যবহার করা হতো। স্থানীয়ভাবে জনশ্রুতি আছে যে, গোবিন্দশ্রী গ্রামের মৌলভী কুদরত উল্লাহ মনু নদীর তীরে আটারো শতকের প্রথম দশকের দিকে একটি ছোট্ট বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে বাজারটি তাঁর নামের ‘মৌলভী’ উপাধিযোগেই নাম ধারণ করে মৌলভীবাজার। আবার ভিন্নমতে, ‘মলয়’ বা ‘মলই’ নামের জনৈক পাটনি মনু নদীতে মাছ ধরে যে স্থানে বসে বিক্রি করতো কালক্রমে সে স্থানটি ‘মলয়বাজার’ বা ‘মলইবাজার’নামে পরিচিতি লাভ করে। জায়গাটি ছিল মৌলভী কুদরত উল্লাহর বংশের। পরবর্তীকালে তিনি সেটার নাম পরিবর্তন করে তাঁর নামের উপাধিযোগে এটির নামকরণ করেন ‘মৌলভীর হাট’। অর্থাৎ এটা তখন নিত্যপ্রয়োজনীর দ্রব্যাদির বাজার ছিল না। সপ্তাহ অথবা পক্ষকালে একদিন হাট বসতো। এরও পরে এটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়ে ‘মৌলভীবাজার’ নাম ধারন করে। ‘মলইবাজার’ থেকে ‘মৌলভীর হাট’ নামকরণে হিন্দুসম্প্রদায়ও কোনো আপত্তি করেননি। একজন পাটনির নামে বাজারের নাম হবার চাইতে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের নামে বাজারের নামকরণ হওয়াটাকে তাঁরা অনেক ভালো মনে করেছিলেন।
বলা বাহুল্য, এটা ইতিহাস নয়, জনশ্রুতি। তবে ইতিহাসেরও উপাদান আছে। কারণ, স্থানীয় সাধারণ লোকেরা বাজারটিকে এখনও ‘মলইবাজার’ বলে থাকেন, এবং বাজারটি এতো পুরনো বলেও মনে হয়না তা আগেই বলেছি। খুবসম্ভব আটারো শতকের মধ্যভাগে অথবা তারও পরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। এ ধারণার কারণ একটি উদাহরণ দিয়ে পরিস্কার করা যাক। আমরা জানি যে, ১৭৭৯ সালে (১১৭৮ বাংলা সনে) বানিয়াচঙের জমিদার আমেদ রেজা শীবপাশা নামক স্থানে একটি হাট বসান এবং সেটির নামকরণ করেন নবীগঞ্জ। নবীগঞ্জ নামক এ হাট প্রতিষ্ঠার মাত্র এগারো বছরের মাথায়, ১৭৯০ সালের ২৬ নভেম্বর জন উইল্স যখন সিলেটের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ত্রিশটি থানার প্রস্তাব করেন। তখন তাঁর সে প্রস্তাবিত থানার তালিকার ছয় নাম্বারে ছিল নবীগঞ্জ। এর পর থেকে বার বার থানার সংখ্যা বাড়ানো-কমানো হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালের আগে ‘মৌলভীবাজার’ নামে কোনো থানার নাম ব্রিটিশ আমলের কোনো রেকর্ডপত্রে পাওয়া যায় না।
১৮৭৬ সালের ৬ মে আসাম গেজেটে প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সিলেট জেলাকে - সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, লস্করপুর এবং লাতু (বা করিমগঞ্জ)-এ চারটি মহকুমায় ভাগ করা হয়। কিন্তু ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত প্রজ্ঞাপনটি কার্যকর হয়নি। তখন বর্তমান মৌলভীবাজার জেলাধীন এলাকাটি ছিল সিলেট সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত।
উল্লেখ্য যে, কালেক্টর জন উইল্স সিলেটে জেলার জরিপ শেষে ১৭৯০ সালের জানুয়ারি মাসে কসবে সিলেট বাদে জেলার ১৮৬টি পরগনাকে ১০টি রাজস্ব-জেলায় ভাগ করেন। রাজস্ব-জেলাগুলো ছিল: ১. পারকুল (সিলেট) ২. তাজপুর ৩. রসুলগঞ্জ ৪. লাতু হারগাজিয়া (হিঙ্গাজিয়া) ৫. রাজনগর ৬. নোয়াখালি (বর্তমান মৌলভীবাজার) ৭. নবীগঞ্জ ৮. শঙ্করপাশা ৯. লস্করপুর, ও ১০. প্রতাপগড়।
তখন নোয়াখালি (বর্তমান মৌলভীবাজার) রাজস্ব জেলাধীন এলাকাটি ছিল -চৌয়াল্লিশ, বালিশিরা, সাতগাঁও, চৌতলী, গিয়াসনগর (বা গয়াসনগর), চৈতন্যনগর ও আথানগিরি পরগণা নিয়ে গঠিত। রাজনগর রাজস্ব জেলাধীন পরগণাগুলো ছিল- ইটা, শমসেরনগর, আলীনগর, ইন্দেশ্বর, পানিসাইল, ভানুগাছ ও আদমপুর পরগণা নিয়ে এবং হিঙ্গাজিয়া রাজস্ব জেলাধীন পরগনাগুলো ছিল - কানিহাটি, বরমচাল, ভাটেরা, পাথারিয়া, ইয়াকুবনগর ও লংলা।
১৮৮০ সালের ১১ জুন এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সিলেট জেলাকে ১৮৭৭ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইনের, সেকশন ৫-এ, - পাঁচটি সাব-ডিসট্রিক্টটে ভাগ করা হয়। সাব-ডিসট্রিক্টগুলো ছিল - সিলেট সদর, রাজনগর, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ। তখন রাজনগর সাব-ডিসট্রিক্ট-এর মধ্যে রাখা হয় মাত্র দুটি থানা - রাজনগর ও নোয়াখালি এবং এর সদর দফতর করার সিদ্ধান্ত হয় ‘মৌলভীর হাট’। কিন্তু এ প্রজ্ঞাপনও আলোর মুখ দেখেনি। একই সালের (১৮৮০ সাল) ১ সেপ্টেম্বর আরেকটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সিলেট জেলাকে ১৬টি থানায় ভাগ করে সেগুলোর সীমানা পুর্ননির্ধারণ করা হয়। তখন সিলেট বা সদর সাব-ডিভিশনের আওতাধীন থানাগুলো ছিল: সিলেট, কানাইঘাট, বালাগঞ্জ, হিঙ্গাজিয়া, রাজনগর ও নোয়াখালি।
পরবর্তী সময়ে সিলেট সদর মহকুমা অত্যধিক বড়ো বিবেচনায় ১৮৮২ সালের ১ এপ্রিল উত্তর সিলেট ও দক্ষিণ সিলেট- নামে দুটো মহকুমায় ভাগ করা হয়। কিন্তু কোনো অফিসঘর না থাকায় দক্ষিণ সিলেট মহকুমায় কোনো কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে তা ঘোষণার মধ্যেই থেকে যায়। দক্ষিণ সিলেটের সাব-ডিভিশনের কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৮৪-৮৫ অর্থ-বছরে। তখন সাব-ডিভিশনাল অফিসার নিয়োগ লাভ করেন - মি. জে. কে. দে। ১৮৮৭ সালে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঈশান চন্দ্রপত্রনবিস। ১৮৮৮ সালে অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার পদে যোগদান করেন মি. আর. আর. পোপ (জ. জ. চড়ঢ়ব, ঈ. ঝ.) এবং মুন্সিফ মি. আশুতোশ ব্যানার্জি। ১৮৯১ সালে পোপের স্থলাভিষিক্ত হন মি. জে. এল. হ্যারল্ড, সি. এস.; ১৮৯২ সালে মি. এফ. সি. ফ্রেঞ্চ, ১৮৯৩ সালে মি. এফ. সি. হ্যান্নিকার (১৮৯৪-৯৫); ১৮৯৬ সালে, মি. ডব্লিউ. জে. রিড (১৮৯৬-৯৮)।
১৮৯৭ সালের সিলেটে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। এ ভূমিকম্পে দক্ষিণ সিলেট মহকুমা সদরে যে দু’চারটি অফিস ভবন নির্মাণ হয়েছিল তাও মাটিতে মিশে যায়। ফলে মৌলভীবাজারের নগরায়নের কাজটি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে। ভূমিকম্পের পরে আবারও শুরু হয় বিভিন্ন অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ। এর সূচনা হয় সাব-রেজিস্টার অফিস ও লোক্যাল বোর্ড অফিস নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এ দুটি অফিসের নির্মাণ কাজ ৫,০৩১ রুপি ব্যয়ে শেষ হয় ১৮৯৮ সালে।
এর পরে মহকুমা অফিসার নিয়োগ লাভ করেন - যথাক্রমে -মি. এস. জি. হার্ট, (১৯৯৯-১০০২); মি. জন গ্রাহাম ডানলপ, (১৯০৩-১৯০৪); এবং মি. জি. ই. লামবর্ন (১৯০৫-১৯০৯). ১৯০১ সালে মৌলভীবাজার শহরের লোকসংখ্যা ছিল ২,৪৮১ জন। ১৯৫১ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৫,৯৬৭ জনে। এর মধ্যে ৩,৭০১ জন পুরুষ এবং ২,২৬৬ জন মহিলা।
১৯০৫ সালে প্রশাসনিক রিপোর্টে বলা হয়:
In the year 1905, for general administration purpose, the district was divided into five subdivisions. North Sylhet was under immidate charge of the Deputy Commissioner, Karimganj and South Sylhet were entrusted to Assistant Magistrates who were almost invariably Europeans, Habiganj and Sunamganj entrusted to Magistrates who were usually local officers.
সেকালে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নদী। নদীকে কেন্দ্র করেই শহর-বন্দর গড়ে উঠতো। মনু ও ধলাই নদী মাধ্যমে মহকুমার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সুবিধাজনক স্থান হিসেবে মৌলভীর হাট নামক ছোট্ট হাট থেকে প্রায় এক মাইল দূরে মহকুমার কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়া হয়। ১৮৯৭ সালের ১০ মে দক্ষিণ সিলেট মহকুমার সীমা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এখানে কৌতুহলের বিষয় যে, দক্ষিণ সিলেট মহকুমা মৌলভীর হাটের অনতিদূরে স্থাপিত হলেও তখন পর্যন্ত ‘মৌলভীর হাট’ বা ‘মৌলভীবাজার’ নামে কোনো থানা ছিল না।
বি. সি. অ্যালেনের দেয়া তথ্যানুসারে মৌলভীবাজার থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ সালে। তখন দক্ষিণ সিলেট (বা দক্ষিণ শ্রীহট্ট) মহকুমার প্রাচীন তিনটি থানা - রাজনগর, নোয়াখালি ও হিঙ্গাজিয়াকে নতুন তিনটি থানা ও দুটি পুলিশ ফাঁড়িতে বিন্যস্ত করা হয়। এ নতুন থানাগুলো ছিল - কমলগঞ্জ, কুলাউড়া ও মৌলভীবাজার, এবং পুলিশ ফাঁড়িগুলো ছিল - রাজনগর ও শ্রীমঙ্গল। এ সময় নোয়াখালি ও হিঙ্গাজিয়া থানা দুটোর স্থান পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় এবং রাজনগর থানাকে পুলিশ ফাঁড়িতে রূপান্তরিত করা হয়। অর্থাৎ তখন নোয়াখালি থানাকে থানাবাজারের নিকট থেকে মলইবাজার বা মৌলভীর হাটে নিয়ে এসে এটির নামকরণ করা হয় মৌলভীবাজার থানা। যদিও অ্যাডওয়ার্ড অ্যালবার্ট গেইট, তাঁর লেখা এবং ১৯০৬ সালে প্রকাশিত এ হিস্ট্রি অব আসাম গ্রন্থে মৌলভীবাজারকে মহকুমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তখন পর্যন্ত মহকুমার নাম ছিল দক্ষিণ সিলেট। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্ধনীর মধ্যে মৌলভীবাজারও লেখা হতো ।
১৯২২ সালের ১০ জানুয়ারি, ১৭৬ নং জি. জে. নোটিফেকেশনের মাধ্যমে সিলেটে জেলার অন্যান্য থানার মতো মৌলভীবাজার থানাও স্থায়ীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।
নোয়াখালি রাজস্ব জলা ও থানার অবস্থান সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়তো অজ্ঞাত। এটি অবস্থান ছিল বর্তমান কামালপুর ইউনিয়নের অজমর্দ গ্রামের (বর্তমানে গ্রামটির নাম আজমনি) নিকটবর্তী থানাবাজারের পাশে। নোয়াখালি রাজস্ব জেলা ও থানা উঠে গেলেও বাজারটি থানাবাজার নামে আগে যেমন পরিচিত ছিল, এখনও ইতিহাসের সাক্ষি হয়ে আছে।
উল্লেখ্য যে, বর্তমান “নোয়াখালির” প্রাচীন নাম ছিল “ভুলুয়া” পরবর্তীকালে সেটির নামকরণ করা হয় “নোয়াখালি”।
লেখক : ফারুক আহমদ
(বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, “আত্মঘাতী বাঙালি ও অন্যান্য প্রবন্ধ”)
মীর্জা ইকবাল
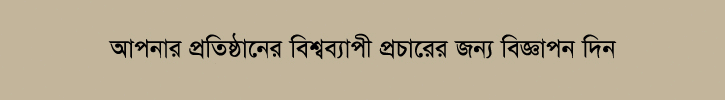
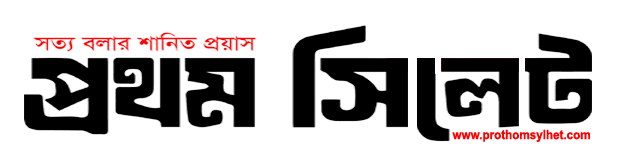
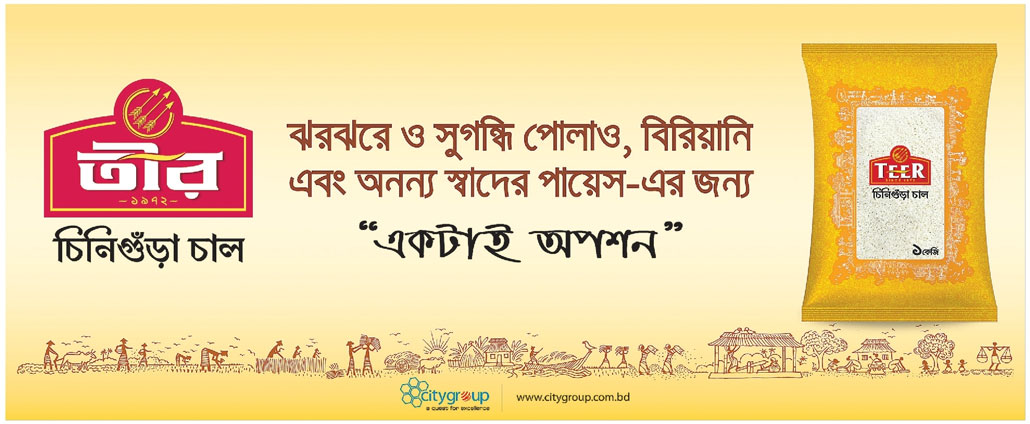
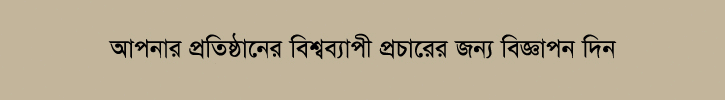
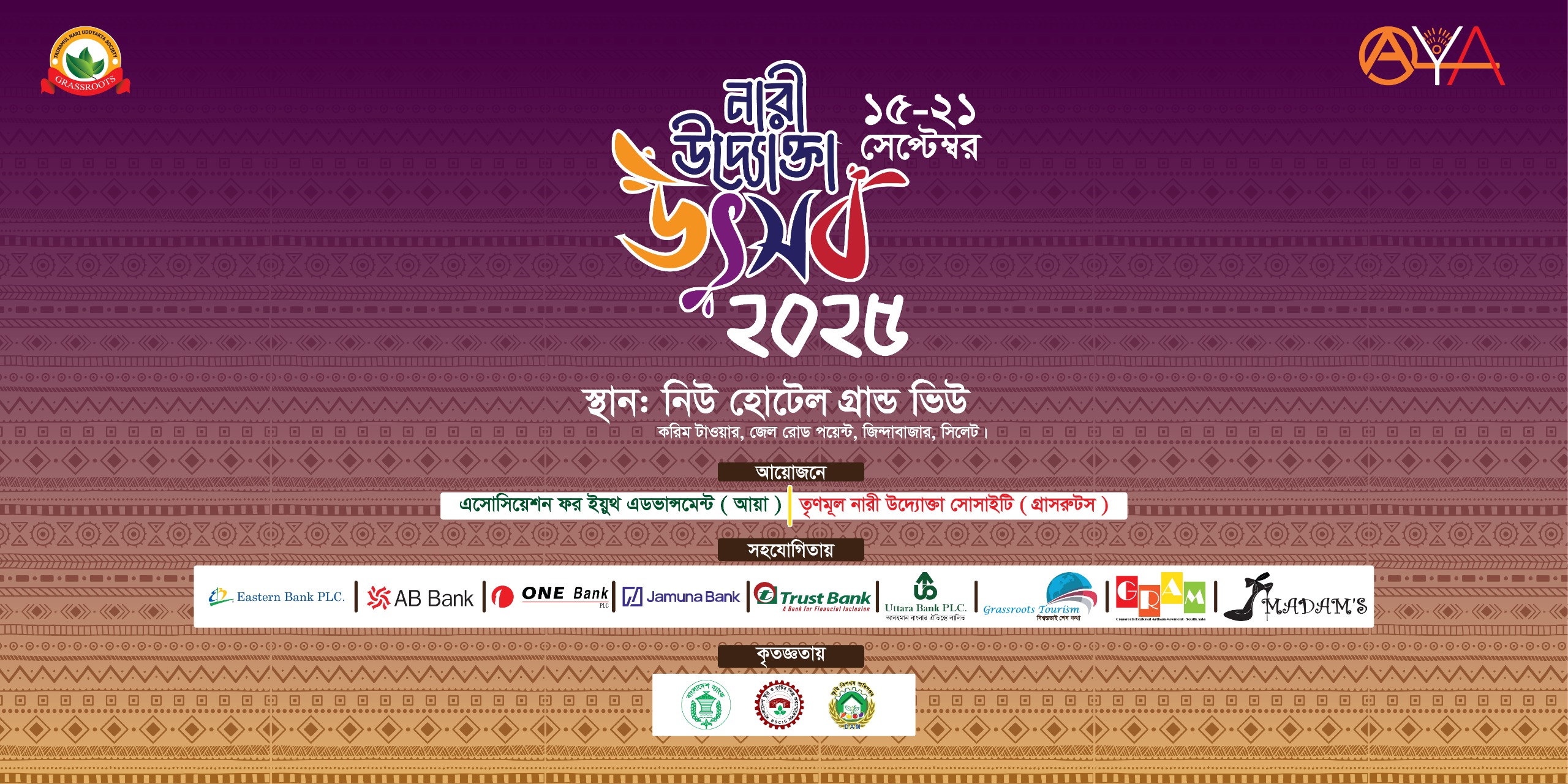


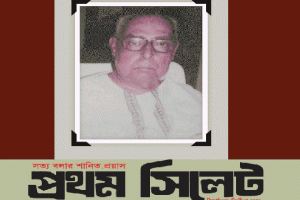
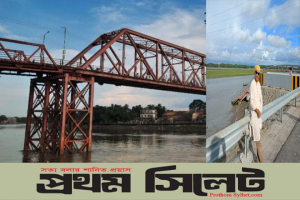
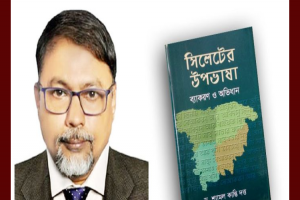
মন্তব্য করুন: