বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য: জেগে থাকে নশ্বর জীবন
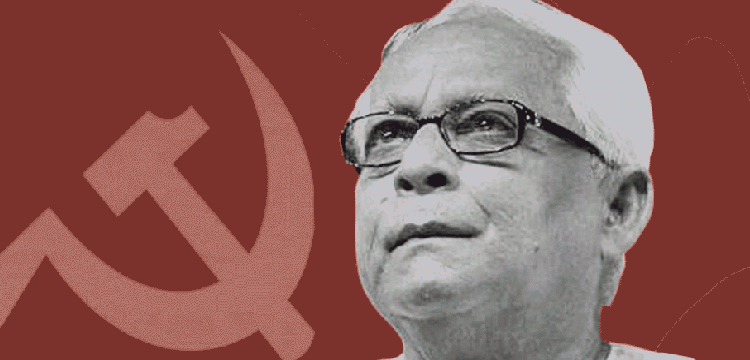
জীবনের প্রায় অর্ধেকটা সময় দক্ষিণ কলকাতাতে কাটালেও মনে প্রাণে তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার মানুষ। পরিবার সূত্রে অবিভক্ত ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার ধারা থাকলেও উত্তর কলকাতা ছিল তাঁর , 'মনের আনন্দ, প্রাণের আরাম।' রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও তাঁর এখানেই, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক চেতনার ও। ' সুকান্ত কাকা' তাঁর সেভাবে ব্যক্তি স্মৃতিতে ধরা ছিল না। ছিল কেবল সুকান্ত কাকার অসুস্থতা ঘিরে বাড়ির মানুষদের ব্যস্ততা। তাই সুকান্ত ভট্টাচার্যের বন্ধু কলিম শরাফির সঙ্গে দেখা হলেই শিশুর মতো জানতে চাইতেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর সুকান্ত কাকার কথা। আসলে কবি সুকান্ত, বুদ্ধবাবুর মননকে প্রথম জীবনেই যেভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, তারই রেশ কিন্তু তাঁর সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রতি অমন প্রবল অনুরাগ ।
'৭৭ সালে প্রথম যখন তিনি মন্ত্রী হলেন তখন 'পশ্চিমবঙ্গ ' পত্রিকায় নতুন মন্ত্রীদের ছবি-সহ জীবন পঞ্জী প্রকাশিত হয়েছিল। ডান হাতটা চেয়ারে হেলান দেওয়া অংশে উঁচু করে রাখা-বুদ্ধবাবুর সেই ছবিটা আজ বড্ড মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, দেবব্রত বিশ্বাসকে তাঁর ট্রায়ঙ্গুলার পার্কের ভাড়া বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবার ভাবনা যখন বাড়িওয়ালা করেন, কি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বুদ্ধবাবু। ওই সমস্যার সমাধান যে 'পোলাপান মন্ত্রী' বুদ্ধদেববাবু করতে পারবেন, দেবব্রত সেটা প্রথমে ভাবতেই পারেননি। সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানের আগেই অবশ্য দেবব্রত প্রয়াত হন। কিন্তু বুদ্ধবাবুর উদ্যোগে যে সাময়িক স্বস্তি দেবব্রত পেয়েছিলেন, সেই 'পোলাপান মন্ত্রী'-র কথা কিন্তু যাঁরাই তাঁর কাছে তখন আসতেন, মুক্তকন্ঠে শিল্পী বলতেন।
সত্যজিৎ রায় গুরুতর হার্টের অসুখে পড়লেন। সিঁড়ি ভাঙা ডাক্তারের বারণ। তাঁর ফ্ল্যাটে লিফট বসানো--সব উদ্যোগ রাতারাতি নিলেন বুদ্ধবাবু। সত্যজিৎ রায়ের বাইপাস অপারেশন দরকার। ভারতে তখন ও ওই ধরণের অপারেশনের খুব ভাল পরিকাঠামো ছিল না। সত্যজিৎ নিজে এবং তাঁর কাছের মানুষেরা যোগাযোগ করলেন জগৎ বিখ্যাত কার্ডিও থোরাসিক সার্জেন ডাক্তার ডেন্টন কুলির সঙ্গে হিউস্টনে। কিন্তু চিকিৎসা, অপারেশন, যাওয়া- আসা, সব মিলিয়ে যা খরচ, সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে সেটা বহন করা সম্ভব নয়। সবটা জেনে বুদ্ধদেববাবু তৎকালীন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমেরিকার হিউস্টনে গিয়ে সত্যজিৎ রায়ের বাইপাস সার্জারির যাবতীয় খরচ বহনের সব ব্যবস্থা করলেন। বিজয়া যায় নিজেও এই পর্বের কথা বিস্তারিত ভাবে, 'আমাদের কথা'-তে লিখে গিয়েছেন।
সুনীল, শক্তি, শামসুর রাহমানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল বন্ধত্বের। শামসুর তাঁর কবিতা সংগ্রহ বুদ্ধদেবকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নন, আমার কবিতার পাঠক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে।' তাঁদের আড্ডা ছিল সে সময়ের বাঙালির অন্যতম সেরা আড্ডা। বুদ্ধদেব রাজনীতির মানুষ। কিন্তু সুনীল, শামসুরদের সঙ্গে আড্ডার কালে সেই রাজনীতির মানুষটাই হয়ে যেতেন পরিপূর্ণ সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। সিগারেটের ধোঁওয়া আর চায়ের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য, কবিতা ছাপিয়ে কখন যে তাঁরা পাড়ি দিতেন বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায়, মার্কেজ হয়ে চলে আসতেন সদ্য প্রকাশিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ' খোয়াবনামা' তে -- শামসুর বলছেন, উপ মুখ্যমন্ত্রীকে নয়, তাঁর বন্ধু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ইলিয়াসের চিকিৎসা ঘিরে আর বুদ্ধদেব জানতে চাইছেন শামসুরের কাছে কবি বুদ্ধদেব বসুর কথা-- এসবের সাক্ষী থাকা , আজ মনে হচ্ছে, এ জীবনেই এসব ঘটেছিল তো?
যখন তিনি প্রশাসনের অনেকটাই সামলাচ্ছেন, তখন ও তাঁর নিত্য সঙ্গী বই। আর যখন প্রশাসনের পুরোটা সামলাচ্ছেন, তখন ও তাঁর নিত্য সঙ্গী বই। আবার 'প্রাক্তন' হয়ে যাওয়ার পরে, দলীয় কার্যালয়ে, বিকেলে তাঁর অতি প্রিয় জলখাবার, মুড়ি আর তেলেভাজা খেতে খেতেও উল্টে চলেছেন সেই বইই।
বুদ্ধদেববাবুর ব্যক্তি জীবনে মেটিরিয়ালিস্টিক কোন বিষয়ে আকর্ষণ ছিল? এই প্রশ্ন উঠলে, এককথায় বলতে হয়, সিগারেট আর বই।কোনটাকে আগে রাখবেন? বইকে? না, সিগারেট কে? - প্রশ্ন করলে কিছুতেই উত্তর দিতেন না। অদ্ভূত একটা স্বর্গীয় হাসি হাসতেন। নতুন কোনও বই প্রকাশিত হলে, তাঁর হাতে তুলে দিলে খুব আনন্দ পেতেন। সাগ্রহে পড়তেন। কিন্তু পড়া হয়ে গেলে, বইটা ব্যক্তি সংগ্রহে রাখতেন না। দিয়ে দিলেন পার্টি অফিসের লাইব্রেরিতে। সর্বার্থে সততার জায়গাতে এমনটাই ছিলেন তিনি।
দেশের নানা রাজনৈতিক টালমাটাল তাঁকে কাব্যের সূক্ষ্ম দিক ঘিরে খুব একটা চর্চা করতে দেয়নি, এমন একটা দুঃখ ছিল শামসুর রাহমানের। বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে নিজের সেই অনুভূতির প্রসঙ্গ একদিন তুললেন শামসুর। বুদ্ধদেব পরপর এক নাগাড়ে আবৃত্তি করে গেলেন শামসুরের একুশের প্রেক্ষিতে লেখা , 'বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে' থেকে শুরু করে,' আসাদের শার্ট' হয়ে, 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কবিতাগুলো। মাঝে অবশ্যই বললেন , 'বন্দিশিবির থেকে' কাব্য গ্রন্থের সেই বিখ্যাত যমজ কবিতা দু'টি, 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' আর,' স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশী গান'-- বিরামহীন ভাবে আবৃত্তি করে গেলেন।
শামসুর অবাক বুদ্ধদেবের স্মৃতি শক্তি দেখে। আর তখন বুদ্ধদেব বলে চলেছেন কবিকে, বলুন- আজ হোক বা আগামীতে হোক মানবতা আক্রান্ত হলে, মনুষ্যত্বের অবনমন ঘটলে, সভ্যতা আবার ও সঙ্কটের মুখে পড়লে দেশ- কাল নির্বিশেষে আপনার এসব কবিতার কোন শব্দটার গুরুত্ব সে কালেও , ওকালের মতো থাকবে না? পাঠকের তো মনে হবে, হয়ত কাল রাতে বসে কবি এসব কবিতা লিখেছেন।বুদ্ধদেবের বিশ্লেষণে অবাক শামসুর। যদিও তাঁর অবাক হওয়ার তখন ও অনেক বাকি রয়েছে।
বুদ্ধদেব বলে চলেছেন; এই যে আপনি আপনার দেশের সঙ্কটকে বনপোড়া হরিণীর কান্না- এই উপমার ভিতর দিয়ে মেলে ধরেছেন, এই ইমেজারি কি কেবল একটা ক্ষনিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের জের? যতদিন মানুষের অধিকার ঘিরে লড়াই থাকবে, ক্ষুধা ঘিরে কান্না থাকবে, মানুষ কি ততদিন বনপোড়া হরিণীর আর্তনাদ করবে না দেশে?
একজন রাজনীতিকের মুখে এই ব্যাখ্যা শোনবার পর শামসুর রাহমান কিন্তু নিজের সৃষ্টিতে তাৎক্ষনিকতার প্রয়োগ ঘিরে নিজেই একটু খুঁতখুঁতে ভাবনা নিয়ে চলতেন, সেই ভাবনা সমূলে উৎপাটিত করেছিলেন। বুদ্ধবাবু প্রথম যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতিবাবুর অবসরের পর, নিজের হাতে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে নিজেই সেকথা জানিয়েছিলেন কবি। সে চিঠি ঢাকা থেকে বয়ে এনে পৌঁছে দিয়েছিলাম তাঁর হাতে। আজ একটাই আফশোষ জাগে, সে চিঠির কোনও চিত্রলিপি রাখি না। সেটা থাকলে আগামী প্রজন্ম কবি শামসুরের কলমে কবিতার নিবিড় পাঠক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নতুন করে চিনতে পারত।
বুদ্ধবাবুর রসবোধের সূক্ষতা ছিল অতি উচ্চমানের। একটা ঘটনা বলি। এপিজে আবদুল কালাম তখন দেশের রাষ্ট্রপতি। পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছেন। প্রটোকল মোতাবেক রাজ্যের সেই সময়ে যুবকল্যাণ মন্ত্রী মহঃ সেলিম সঙ্গী থাকবেন রাষ্ট্রপতির। একজন উচ্চপদস্থ আমলা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুকে বললেন, রাষ্ট্রপতি তো কাজ পাগল মানুষ। কাজের ব্যস্ততায় খাওয়া দাওয়াই ভুলে যান। সেলিমের লাঞ্চের খুব অসুবিধা হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী এতটুকু না হেসে , আরও খানিকটা গাম্ভীর্য টেনেই বললেন; সেলিম তো ড্রাই ফ্রুট খায়। পাশে থাকা সেলিম ও অবাক , এতএত কাল পরে একটা ছোট্ট ঘটনাকে মনে রেখে এভাবেও রসিকতা করতে পারেন তাঁর বুদ্ধদা, এই কথা ভেবে।
ঘটনাটা এইরকম-- সেলিমের মামা বাড়ি মধ্য কলকাতায়। তাঁর মামাদের ছিল ড্রাইফ্রুটের ব্যবসা। তখন সেলিম ফায়ার ব্রান্ড যুব নেতা। মামার বাড়ির দিকে রাজনীতির প্রয়োজনে গেলেই একবার ঢুঁ মারতেন। আর তাঁর মামাতো বোনেরা পকেট ভরে দিতেন মেওয়াতে। সেলিম ও অকাতরে কমরেডদের মধ্যে সেসব বিলোতেন।
কথাটা শুনেছিলেন বুদ্ধবাবু। তখন কিচ্ছু বলেননি অনুজপ্রতিম সেলিমকে। কিন্তু এত এত বছর পরে ভাইয়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে নিজেকে আরও বেশি গম্ভীর করে সেকথা বলে বসলেন সরকারি আমলাকে। সেলিম সংসদে হিন্দিতে বেশি বক্তৃতা করুন- এটা মন থেকে খুব একটা চাইতেন না বুদ্ধবাবু। চাইতেন সেলিম ইংরেজিতেই বলুন। কিন্তু সেলিম চাইতেন, নিজের বক্তব্য আম জনতার কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে। তাই তাঁর ইংরেজিতে বলবার থেকে বেশি পক্ষপাতিত্ব ছিল হিন্দিতে বলবার দিকেই।
সেলিমের এই যুক্তি কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন বুদ্ধবাবু। এমন টাই ছিল তাঁর যুক্তিবোধের প্রতি শ্রদ্ধা। নিজের মতোই ঠিক, অন্যের যুক্তিকে গুরুত্ব দেব না- এটা বুদ্ধবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। কেবল আবেগ নয়।সঠিক তথ্য আর যুক্তির প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব।
সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ছিল তাঁর তীব্র। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অব্যবহিত আগে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে বক্তৃতা করছেন সেলিম। গাড়িতে যেতে যেতে সেটা শুনলেন বুদ্ধবাবু। তারপর সেই বক্তৃতাকে আরও শানিত করবার প্রয়োজনীয় টিপস দিলেন কমরেডকে। এমনটাই ছিল তাঁর কমরেডদের প্রতি মনোযোগ।
ইস্কুলে পড়াকালীন পুরস্কার পেয়েছিলেন অন্নদাশঙ্করের , 'পথে প্রবাসে।' সেই থেকে অন্নদাশঙ্করের প্রতি তৈরি হয়েছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।' ৭৭ সালে প্রথম মন্ত্রী হয়েই অন্নদাশঙ্করের কাছে গেলেন বুদ্ধবাবু। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বাংলা আকাদেমি তৈরি ঘিরে অন্নদাশঙ্করের ভাবনা। সেই সাক্ষাৎতেই বললেন; আমরা যত দ্রুত সম্ভব বাংলা আকাদেমি করব। আপনাকেই নিতে হবে সভাপতির দায়িত্ব।
অন্নদাশঙ্কর তখন নতুন করে কোনো আর প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন না। বুদ্ধবাবু আমাকে বললেন; তোমাকে রাজি করাতেই হবে ওঁকে। অন্নদাশঙ্কর সম্মত হওয়ার পর বাংলা আকাদেমি গঠিত হলে প্রথম বই হল, প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা। অত কম দামে, অত উচ্চমানের বই সে সময়েও দুর্লভ ছিল।
'৯৬ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণ পেলেন অন্নদাশঙ্কর। কিন্তু তখন তাঁর পাসপোর্ট নেই। বিষয়টা তাঁকে জানালাম। বললেন, এক্ষুনি রাইটার্সে চলে এস। যেতেই তাঁর অন্যতম সচিব ভাস্কর লায়েককে বললেন, দু'দিনের মধ্যে ওঁর পাসপোর্ট করে দিলেন।
তখন ভারত- বাংলাদেশ পাসপোর্ট হতো। সেই পাসপোর্টের ফর্মে আবেদনকারীকে নিজের চেনা দুজন ভারতীয় নাগরিকের নাম লিখতে হতো। অন্নদাশঙ্কর লিখলেন, জ্যোতি বসু আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।
জ্যোতিবাবুর অবসরের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্রকে। আজন্ম বামপন্থী সুচিত্রা। প্রথম ছাত্রী হিসেবে রবীন্দ্র প্রয়াণের মাত্র কয়েকদিন পরে প্রথম শান্তিনিকেতনে যান। ক্ষিতীশ রায় যাঁকে দেখলেই রেড সেলুট জানাতেন। সেই সুচিত্রা , বাম জামানায় প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর শপথে আমন্ত্রণ পেলেন বুদ্ধদেববাবুর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথের কালে। এই ঘটনাটা সুচিত্রা মিত্রকেও খুব আনন্দিত করেছিল। সুচিত্রা মিত্রের প্রতি বুদ্ধবাবুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ওঁকে কলকাতার প্রথম মহিলা শেরিফের সম্মান ও বুদ্ধবাবুই দিয়েছিলেন। আবার সুচিত্রার আবদার মাঝে মাঝে বুদ্ধবাবুকে বিড়ম্বনাতেও ফেলত।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে কিছু অসততার কাজ করেছিলেন আলো কুন্ডু। কবিপত্নী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল আলো কুন্ডুকে। আলোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে সুচিত্রা খুব বিড়ম্বনাতেও ফেলেছিলেন বুদ্ধদেবকে। বড় অভিমানী ছিলেন মানুষটা। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর নিজস্ব রাজনৈতিক পরিমন্ডলের বাইরের দুনিয়া থেকে তখন ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। একদিন বললাম, শঙ্খ ঘোষ টিউবারকুলোসিসে আক্রান্ত। শুনলেন।
বললাম, ফোন করুন একটু।
উনি কি আমার ফোন ধরবেন?- কন্ঠে গভীর অভিমান।
কেন ধরবেন না?
ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে তাঁর শঙ্খদার গলা ভেসে আসতেই সব অভিমান জল হয়ে গেল। প্রায় আধঘন্টা তাঁরা সেদিন টেলিফোনে কথা বলেছিলেন।
লেখক
গৌতম রায়
কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
সজল আহমদ
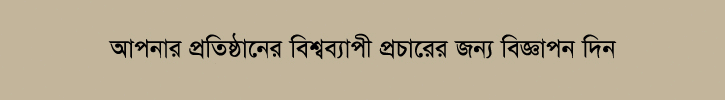
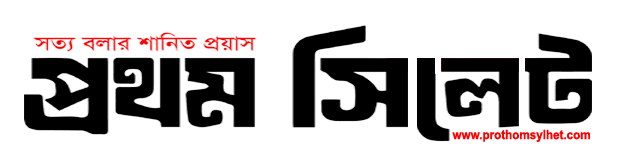
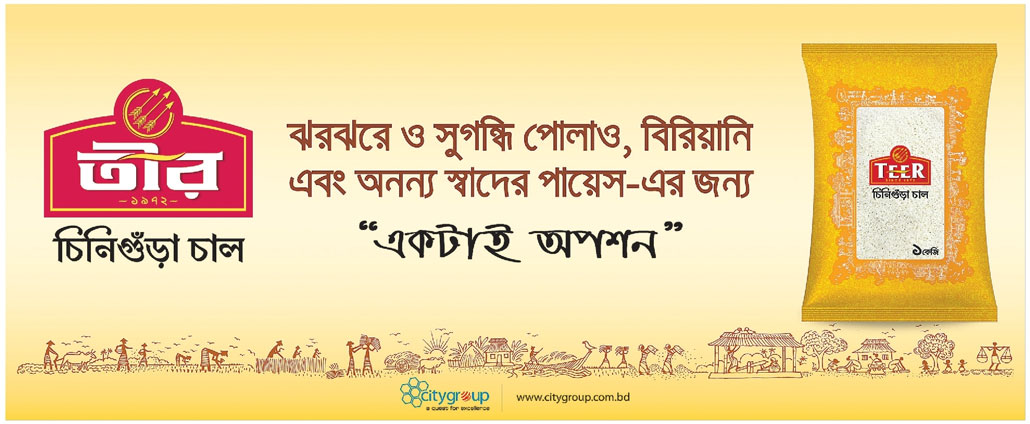
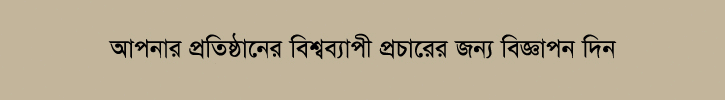
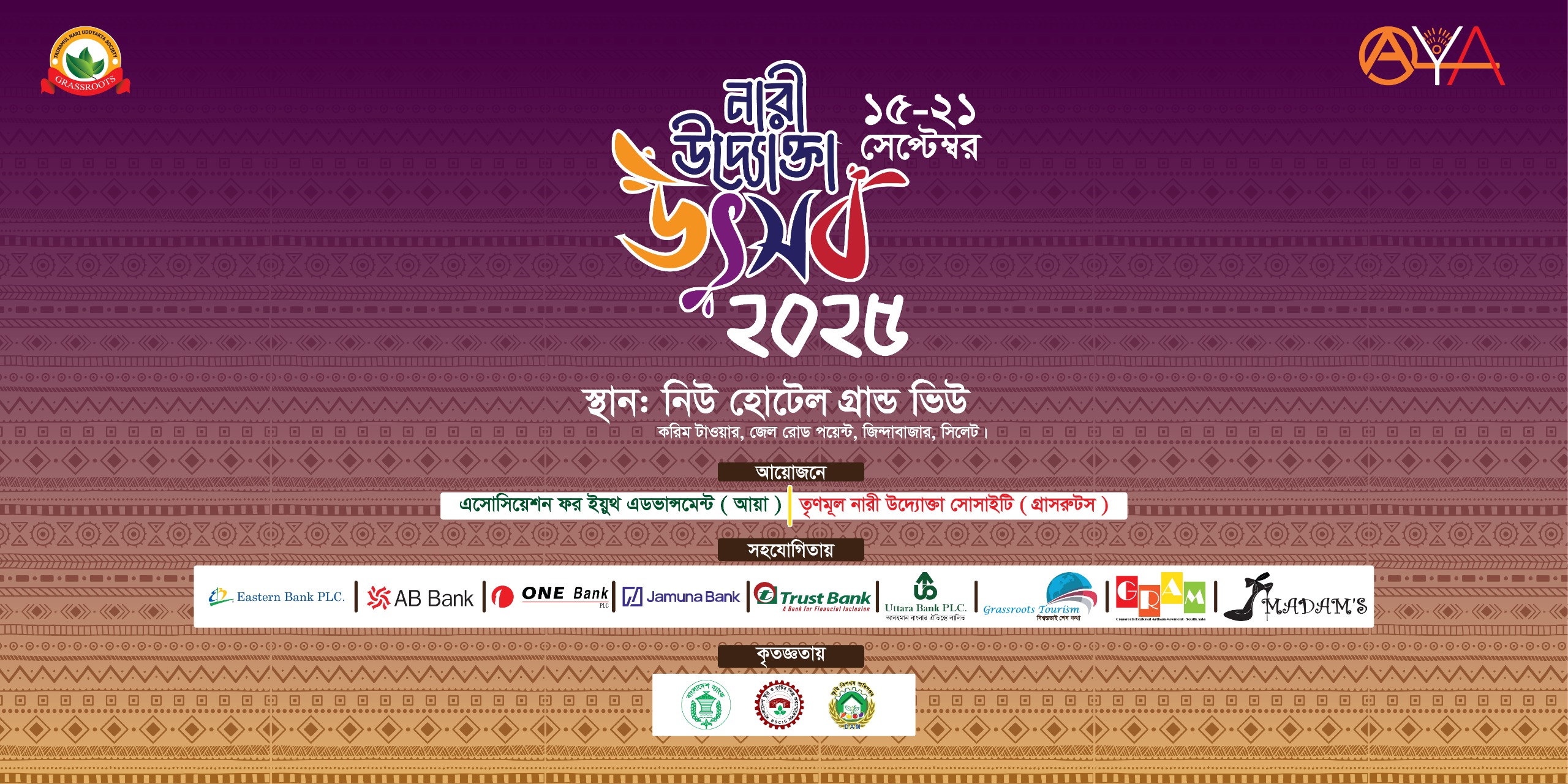


মন্তব্য করুন: